সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান
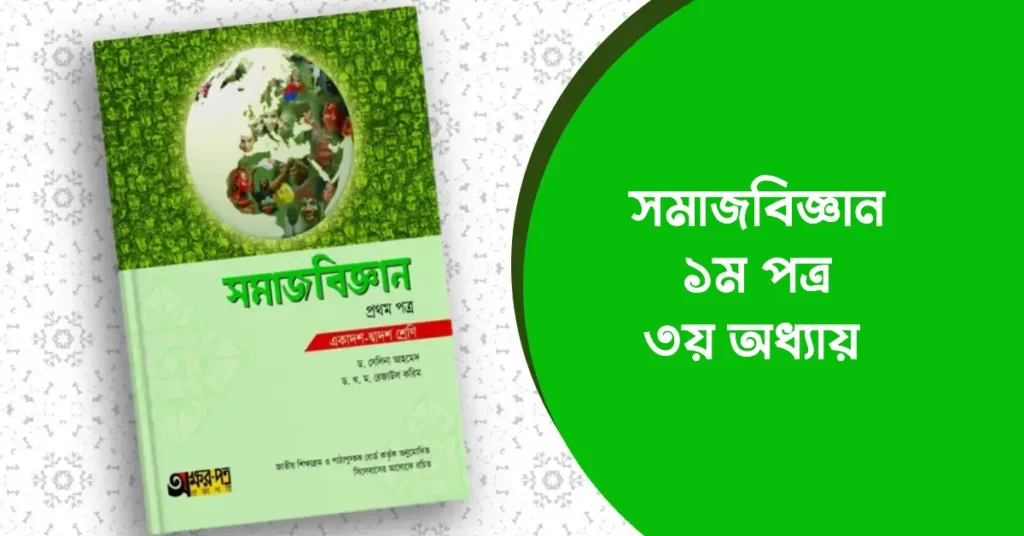
সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র ৩য় অধ্যায়: সমাজ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্রাচীনকাল থেকে শুরু হলেও ঊনবিংশ শতকে এসে সমাজবিজ্ঞান জ্ঞানের একটি আলাদা শাখা হিসেবে উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করে। এরপর থেকে সমাজবিজ্ঞানে বিভিন্ন চিন্তা ও তত্ত্ব নির্মাণ শুরু হয়। এই তত্ত্বগুলো আকস্মিকভাবে তৈরি হয়নি বরং এর পিছনে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন সামাজিক চিন্তাধারা ও সমাজ সম্পর্কিত দর্শন। বর্তমান অধ্যায়ে পথিকৃৎ সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ইব্নে খালদুন, অগাস্ট কোঁৎ, হার্বাট স্পেন্সার, এমিল ডুর্খেইম, কার্ল মার্কস ও ম্যাক্স ওয়েবারের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান
সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান প্রশ্ন-১. আসাবিয়া বলতে কী বোঝ?
উত্তর: ইবনে খালদুনের ‘আল আসাবিয়া’ প্রত্যয়টির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Social Solidarity যাকে বাংলায় বলা হয় সামাজিক সংহতি। এ সংহতিকে ইবনে খালদুন গোত্র সংহতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। খালদুনের মতে, সমাজের ভিত্তিই হচ্ছে গোত্র সংহতি। রক্ত, জাতি ও ধর্ম সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক সংহতি গড়ে ওঠে। তিনি মনে করেন, আসাবিয়ার বিভিন্নতার কারণে সমাজ ও রাজনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। আর এসব পরিবর্তন চক্রাকারে সংঘটিত হয়।
প্রশ্ন-২. গোষ্ঠী সংহতি বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: ইবনে খালদুন সমাজ-শক্তির অন্তর্গত কারণ হিসেবে গোষ্ঠী সংহতি বা সামাজিক সংহতির কথা উল্লেখ করেছেন। সামাজিক সংহতি সম্পর্কে ইবনে খালদুন বলেছেন, সামাজিক সংহতি এক ধরনের আদর্শভিত্তিক অনুভূতি, যা সবাই একত্রে বসবাস করে অনুভব করে এবং সাধারণ দায়িত্বগুলো ভাগাভাগি করে নেয়। এমনকি সাধারণ বিপদ-আপদ এবং ভাগ্যের হেরফেরও তারা একই সাথে মোকাবিলা করে।
ইবনে খালদুন এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, সামাজিক সংহতি সমাজের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ নেতৃত্ব নির্ধারণ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এবং রাজনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে তা সবিশেষ ভূমিকা পালন করে।
প্রশ্ন-৩. অগাস্ট কোঁৎ-কে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয় কেন?
উত্তর: সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য অগাস্ট কোঁৎকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। অগাস্ট কোঁৎ সামাজিক বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি ও দৃষ্টিকোণ তৈরি করেন। সমাজবিজ্ঞানকে একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তার মূল্যবান চিন্তা-দর্শন ও যুক্তি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিল। এসব কারণে অগাস্ট কোঁৎকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করা হয়।
সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান প্রশ্ন-৪. ত্রয়স্তর সূত্রটি ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: অগাস্ট কোঁৎ-এর সমাজ বিকাশের ধারণাটি ‘ত্রয়স্তরের সূত্র’ নামে পরিচিত। সমাজ বিকাশের কারণ সম্পর্কে কোঁৎ-এর অভিমত হলো, সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন আসে জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে আর বস্তুজগতের পরিবর্তন আসে জ্ঞানের উন্নতি বা পরিবর্তনের মাধ্যমে।
তার মতে, মানুষের সকল চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণাসমূহ, জ্ঞানের সকল শাখা এবং পৃথিবীর সকল সমাজসমূহ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে তিনটি স্তর অতিক্রম করে এসেছে এবং বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য । এ তিনটি স্তর হলো ধর্মতাত্ত্বিক, অধিবিদ্যাগত এবং দৃষ্টবাদী স্তর।
প্রশ্ন-৫. দৃষ্টবাদ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: দৃষ্টবাদ একটি দার্শনিক জ্ঞান, যা পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টবাদের মূল বক্তব্য হলো, “ভালোবাসাই নীতি, শৃঙ্খলাই ভিত্তি, প্রগতিই উদ্দেশ্য”। নৈতিক দৃষ্টবাদের সারকথা হলো অন্যের জন্যে বাঁচা। বস্তুত অগাস্ট কোঁৎ জ্ঞানের বিকাশের একটি ইতিহাস তৈরির প্রচেষ্টায় যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন, সে ব্যাখ্যাকে দৃষ্টবাদ বলা হয়েছে।
সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান
প্রশ্ন-৬. হার্বার্ট স্পেন্সারের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: হার্বার্ট স্পেন্সার আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে যে উপাদানগুলোর ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। স্পেন্সার জীবনের শেষদিন অবধি চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন। স্বাভাবিক অধিকারের প্রতি আসক্তি, স্বাভাবিক নিয়ম, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা শাসকের বিরুদ্ধে জেহাদ, যোগ্যতমের উর্ধ্বতনের নীতি— সবকিছুই তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। স্পেন্সার যে আদর্শ সমাজের কথা বলেছেন তা হলো বর্তমানের শিল্পসমাজ। এ সমাজেই মানুষের স্বাধীনতা, সুখ-শান্তি ও জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়।
প্রশ্ন-৭. স্পেন্সার কীভাবে সমাজকে জীবদেহের সাথে তুলনা করেছেন? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: সাদৃশ্য স্থাপনের মাধ্যমে স্পেন্সার সমাজকে জীবদেহের সাথে তুলনা করেছেন। জীবদেহের অঙ্গসমূহের প্রত্যেকটি যেমন পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তা হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরি স্বাধীন ও স্বনির্ভর নয়, তেমনি সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকলেও তা সার্বিক অর্থে স্বাধীন বা স্বনির্ভর নয়।
এক কোষবিশিষ্ট অত্যন্ত সাধারণ এক রকম প্রাণী থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের জীবজগতের বিকাশ ঘটেছে। তেমনি সমাজ আদিম সরল অবস্থা থেকে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান জটিল স্তরে পৌঁছেছে। জীব দেহ এবং সমাজ দেহের বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে এদের কাঠামোগত জঠিলতা বৃদ্ধি পায় এবং দু’য়ের ধ্বংসই অনিবার্য।
প্রশ্ন-৮. স্পেন্সারের আদর্শ সমাজ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: স্পেন্সার তার ‘Social Statics’ নামক গ্রন্থে আদর্শ সমাজ বলতে বুঝিয়েছেন, যে সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। স্পেন্সার মূলত বাস্তব রাষ্ট্রের বিরোধী ছিলেন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতায় বিশ্বাস করতেন।
তার মতে, রাষ্ট্রের কার্যাবলি কেবল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, যাতে মানুষের প্রকৃত অধিকারগুলো সংরক্ষিত হয়। ধর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাম্রাজ্য বৃদ্ধি, সাহায্য প্রদান, মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, ডাক বিভাগ পরিচালনা এমনকি শিক্ষাকেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত না।
প্রশ্ন-৯. জৈবিক সংহতি বলতে কী বোঝ?
উত্তর: এমিল ডুর্খেইমের মতানুযায়ী জৈবিক সংহতি হলো বৈসাদৃশ্যের সংহতি। জৈবিক সংহতি অনুযায়ী এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হতে ভিন্ন এবং ব্যক্তি চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য অনুপস্থিত। জৈবিক সংহতি আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। সমাজে শ্রম বিভাজন বৃদ্ধির সাথে সাথে জৈবিক সংহতির উদ্ভব ঘটে। আধুনিক সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে এবং এ বিভিন্নতার মধ্যেই জৈবিক সংহতি বিদ্যমান।
প্রশ্ন-১০. আত্মহত্যা কী? বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর: এমিল ডুর্খেইম তার ‘Suicide’ গ্রন্থে আত্মহত্যার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, “প্রতিটি স্বেচ্ছামৃত্যু যিনি মারা গেলেন তার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পাদিত কাজ, যা ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক হতে পারে। এ রকম কোনো কাজের ফলে কেউ মারা গেলে সে মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে।” যেমন- কোনো ব্যক্তি যদি নিজের বুকে গুলি করে নিজেকে হত্যা করে তাহলে তা আত্মহত্যা হিসেবে বিবেচিত হবে।
এমিল ডুর্খেইম আত্মহত্যার চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো- মৃত্যু, যে ঘটনার ফলে মৃত্যু হবে তার কারণ হবে ব্যক্তি নিজে, কাজটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে এবং কাজটি ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক হতে পারে।
প্রশ্ন-১১. মার্কস কেন মানবসমাজের ইতিহাসকে শ্রেণি সংগ্রামের ইতি বলেছেন? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: কার্ল মার্কস মানব সমাজের ইতিহাসকে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস বলেছেন। মার্কস সমাজের আদিমকাল থেকে দুটি শ্রেণি চিহ্নিত করেছেন। যথা- ১. মালিক, ২. শ্রমিক বা শোষক ও শোষিত শ্রেণি। এই মালিক বা শ্রমিক আধিপত্যের কারণে সমাজে সংগ্রাম লেগেই থাকে। যার কারণে তিনি নতুন নতুন সংগ্রামের কথা বলেছেন।
যেমন, আদিম যুগে দাস মালিক ও দাসের সংগ্রাম, ভূমি মালিক ও ভূমি গোলাম সম্পর্কের সংগ্রাম, পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সংগ্রাম। এভাবেই প্রতিটি সমাজেই শ্রেণি সংগ্রাম চলেই আসছে বলে মার্কস বলেন, মানবসমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস।
প্রশ্ন-১২. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী?
উত্তর: কার্ল মার্কসের দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূলকথা হলো সমস্ত বস্তু অথবা প্রপঞ্চের বিকাশ হয় দ্বন্দ্বের কারণে। সমাজ পরিবর্তনের মূল কারণও দ্বন্দ্ব। পুরনো অবস্থার সাথে দ্বন্দ্ব চলে তার বিপরীত অবস্থার এবং এরই ফলে একটি সম্পূর্ণ নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। এভাবে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি, বস্তু এবং সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিবর্তন ঘটে। আর এটিই হচ্ছে মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।(আরও দেখুন)
প্রশ্ন-১৩. শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের মূল বক্তব্য কী? বুঝিয়ে বল।
উত্তর: শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের মূল বক্তব্য হচ্ছে, মানব ইতিহাসের প্রতিটি স্তরেই সমাজে বিদ্যমান পরস্পর বিরোধী দুটি শ্রেণির মধ্যে সংগ্রাম চলে। আর এ সংগ্রাম সমাজ পরিবর্তনের মূল কারণ হিসেবে কাজ করে। মার্কসের মতানুযায়ী প্রতিটি সমাজের মধ্যেই দু’টি শ্রেণি বিদ্যমান— শোষক এবং শোষিত।
তিনি বলেন, কোনো একটি সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অনুকূলে কাজ করে। এই শ্রেণিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শোষণ করে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আদর্শগত অবস্থা গড়ে তোলে। ফলে ঐ শ্রেণিটি বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চায় না বরং টিকিয়ে রাখতে চায়। অন্যদিকে, শোষিত শ্রেণিটি সবসময় বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার বিপক্ষে থাকে। মার্কসের মতে, এই দুই মারমুখী শ্রেণির সংগ্রাম সামাজিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।
প্রশ্ন-১৪. এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: কার্ল মার্কস ‘এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা’ তত্ত্ব দ্বারা প্রকৃতিগতভাবে ভিন্নতর এশিয়ার সমাজব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন। এশীয় উৎপাদন পদ্ধতিতে দাস, ভূমিদাস, মজুর শ্রমিকরা কখনো পাশ্চাত্যের মতো শ্রেণি গড়ে তুলতে পারে নি এবং তারা সবাই ছিল রাষ্ট্রের অধীনস্থ। তবে এশীয় উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রেণি সংগ্রামের রূপ কী, সে সম্পর্কে মার্কস কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি।
প্রশ্ন-১৫. ‘আমলাতন্ত্র হচ্ছে আইনগত কর্তৃত্ব’— বুঝিয়ে লিখ।
উত্তর: কর্তৃত্ব যখন রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয় তখন সেটাকে বলা হয় আইনগত আমলাতন্ত্র। সকল সুনির্দিষ্ট ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের বা পরিসীমারই একটি নীতিমালা রয়েছে, যেগুলো সাধারণভাবে আইন বা প্রশাসনিক বিধি-বিধানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ আমলাতন্ত্র যখন আইনগত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে তখন সেটিই হয় আমলাতন্ত্রের আইনগত কর্তৃত্ব।
প্রশ্ন-১৬. ওয়েবার কীভাবে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: ম্যাক্স ওয়েবার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে আইনগত দিক থেকে পার্থক্য নির্ণয় করেন। ওয়েবার এর মতে, ক্ষমতা যখন বৈধতা লাভ করে তখন তাকে কর্তৃত্ব বলা হয় বা ক্ষমতার ভিত্তি যদি আইন হয় তখন তাকে কর্তৃত্ব বলা হয়। আবার ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করে। যেমন— রাজার ছেলে রাজা হলে তাকে ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব বলা হয়।
সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান
প্রশ্ন-১৭. আদর্শ নমুনা বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: ম্যাক্স ওয়েবারের সমাজ বিশ্লেষণের পদ্ধতি হলো আদর্শ নমুনা। কোনো সামাজিক প্রপঞ্চ বা ঐতিহাসিক সত্তাকে জানতে হলে বা বিশ্লেষণ করতে হলে তার আদর্শ নমুনা তৈরি করতে হবে। আর এ নমুনা তৈরির জন্য বিজ্ঞানীকে অন্তর্দৃষ্টির আশ্রয় নিতে হবে।
একটি প্রপঞ্চের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও যৌক্তিকতাকে আদর্শ ধরে নিয়ে অন্য প্রপঞ্চকে তার সাথে মিল বা অমিলের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। ম্যাক্স ওয়েবারের ‘আদর্শ নমুনা’ সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির প্রবর্তন। তিনি আমলাতন্ত্র, পুঁজিবাদ, কর্তৃত্ব ইত্যাদিকে ‘আদর্শ নমুনা’ তত্ত্বের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন।
প্রশ্ন-১৮. সম্মোহনী কর্তৃত্ব বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: ম্যাক্স ওয়েবারের মতানুযায়ী ব্যক্তি বিশেষের অসাধারণ ব্যক্তিগত গুণাবলি, আবেগ আপ্লুত মনোভাব, বীরত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তার সংমিশ্রণ যা সাধারণ মানুষকে অতি সহজেই তার অনুসারী করে তোলে, এরূপ ক্ষমতাকেই সম্মোহনী কর্তৃত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।
সম্মোহনী কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি তার অনুসারীদের মধ্যে এমন ধারণার বিকাশ ঘটাবেন যে, তিনি কখনো ভুল করতে পারেন না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্মোহনী কর্তৃত্বের উত্তম উদাহরণ। সম্মোহনী কর্তৃত্ব ব্যক্তির এমন একটি বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যার মাধ্যমে সে অধিকাংশের মনে দাগ কাটতে পারে।
প্রশ্ন-১৯. বিশেষ গুণসম্পন্ন কর্তৃত্ব বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: বিশেষ গুণসম্পন্ন কর্তৃত্ব বা ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্ব হলো সেই কর্তৃত্ব যা ব্যক্তির অসাধারণ গুণাবলি, আবেগ-আপ্লুত মনোভঙ্গি, বীরত্ব ও স্মরণীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত, ইতিহাস এমন কর্তৃত্বের অনেক সাক্ষ্য দেয়। এক্ষেত্রে জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, গান্ধী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যারা বিশেষ গুণসম্পন্ন কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন।
আশাকরি “সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান – সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র ৩য় অধ্যায়” আর্টিকেল টি তোমাদের ভালো লেগেছে। সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র সকল অধ্যায় এর প্রশ্নোত্তর পেতে এখানে ক্লিক করুন। আমাদের কোন আপডেট মিস না করতে ফলো করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেইজ ।
আরও দেখুন:মানুষ কবিতার মূলভাব ও ব্যাখ্যা
আরও দেখুন:সেইদিন এই মাঠ কবিতার ব্যাখ্যা
আরও দেখুন:কপোতাক্ষনদ কবিতার ব্যাখ্যা
আরও দেখুন:পল্লিজননী কবিতার মূলভাব
আরও দেখুন:সমাসের সহজ ব্যাখ্যা
আরও দেখুন: আনন্দধারা প্রশ্নোত্তর – ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি ১ম অধ্যায়
আরও দেখুন: শীত-প্রকৃতির রূপ সমাধান – ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি ২য় অধ্যায়
আরও দেখুন: পলাশের রঙে রঙিন ভাষা সমাধান – ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি ৩য় অধ্যায়
আরও দেখুন: স্বাধীনতা তুমি সমাধান – ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি ৪র্থ অধ্যায়
আরও দেখুন: নব আনন্দে জাগো সমাধান – ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি ৫ম অধ্যায়
আরও দেখুন: আত্মার আত্মীয় সমাধান – ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি ৬ষ্ঠ অধ্যায়
আরও দেখুন: বৃষ্টি ধারায় বর্ষা আসে সমাধান – ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি ৭ম অধ্যায়
আরও দেখুন: টুঙ্গিপাড়ার সেই ছেলেটি সমাধান – ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি ৮ম অধ্যায়
আরও দেখুন: শরৎ আসে মেঘের ভেলায় সমাধান – ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি ৯ম অধ্যায়
আরও দেখুন: হেমন্ত রাঙা সোনা রঙে সমাধান – ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি ১০ম অধ্যায়
আরও দেখুন: বিশ্বজোড়া পাঠশালা – শিল্প ও সংস্কৃতি ৭ম শ্রেণি ১ম অধ্যায় সমাধান
আরও দেখুন: নকশা খুঁজি নকশা বুঝি – শিল্প ও সংস্কৃতি ৭ম শ্রেণি ২য় অধ্যায় সমাধান
আরও দেখুন: মায়ের মুখের মধুর ভাষা – শিল্প ও সংস্কৃতি ৭ম শ্রেণি ৩য় অধ্যায় সমাধান
আরও দেখুন: স্বাধীনতা আমার – শিল্প ও সংস্কৃতি ৭ম শ্রেণি ৪র্থ অধ্যায় সমাধান
আরও দেখুন: বৈচিত্র্যে ভরা বৈশাখ – শিল্প ও সংস্কৃতি ৭ম শ্রেণি ৫ম অধ্যায় সমাধান
আরও দেখুন: কাজের মাঝে শিল্প খুঁজি – শিল্প ও সংস্কৃতি ৭ম শ্রেণি ৬ষ্ঠ অধ্যায় সমাধান
আরও দেখুন: প্রাণ প্রকৃতি – শিল্প ও সংস্কৃতি ৭ম শ্রেণি ৭ম অধ্যায় সমাধান
আরও দেখুন: প্রাণের গান – শিল্প ও সংস্কৃতি ৭ম শ্রেণি ৮ম অধ্যায় সমাধান
আরও দেখুন: চিত্রলেখা – শিল্প ও সংস্কৃতি ৭ম শ্রেণি ৯ম অধ্যায় সমাধান
আরও দেখুন: শরৎ উৎসব – শিল্প ও সংস্কৃতি ৭ম শ্রেণি ১০ম অধ্যায় সমাধান
আরও দেখুন: সোনা রোদের হাসি – শিল্প ও সংস্কৃতি ৭ম শ্রেণি ১১ অধ্যায় সমাধান।